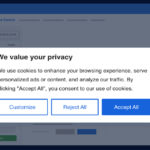উর্বরতা, মাতৃত্ব এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার রক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত প্রান্তিক নারীদের ব্রতপালন
কোনো এক কুয়াশা মাখা সকালে ধানখেতের পাশে একদল নারী জড়ো হয়েছে। হাতে তাদের কলাপাতা, ফুলের মালা, আর মাটির প্রদীপ। তাদের এই উপকরণগুলো নিয়ে এক হওয়া মানে তারা কোনো ব্রত পালন করতে এক হয়েছে।
ব্রত একটি প্রাচীন আচার যা শুধু ধর্মীয় নয়, বাঙালী গ্রাম্য নারীদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ব্রতের মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারের মঙ্গল কামনা করে, স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। কখনো নিজের জন্য, নিজের মঙ্গলের জন্য কোনো বাঙালী নারী ব্রত করে না।
তবে অপরের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি এর পেছনে আরও গভীর কিছু কারণ আছে। এর মধ্য দিয়ে মূলত সংহতি, পরিচয়, আর নিজেদের শক্তির প্রকাশ ঘটায় বাঙালী নারীরা।
বাঙালী সমাজে, বিশেষ করে প্রান্তিক নারীদের জন্য, ব্রত পালন শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি তাদের আত্মপরিচয় গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।
ব্রত : একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের গল্প
বাংলার গ্রাম্য নারীদের ব্রত পালনের ইতিহাস প্রাচীনকালে প্রোথিত। এই আচারগুলোর উৎপত্তি লোকাচার ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। গ্রামের নারীরা প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ধরে রাখতে, ফসলের সমৃদ্ধি কামনা করতে, এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য ব্রত পালন করত। যেমন, শীতলা ব্রত পালন করা হতো সন্তানদের রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখায় ব্রতকে বর্ণনা করেছেন এভাবে-
“কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত”।
এই কামনার মধ্যে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, নারীদের আশা, স্বপ্ন, এবং সংগ্রামের প্রতিফলনও রয়েছে। রয়েছে এক উদার মানসিকতা, যার মধ্য দিয়ে নারীরা শুধু স্বামী-সন্তানের, পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনা করে থাকে।
এই ব্রতগুলোর মধ্যে কিছু শাস্ত্রীয়, যেমন একাদশী বা শিবরাত্রি, আর কিছু অশাস্ত্রীয় বা ‘মেয়েলি ব্রত’, যা মূলত গ্রামের নারীরা পালন করে। কুমারী মেয়েদের জন্য পুণ্যিপুকুর ব্রত বা বিবাহিত নারীদের জন্য জামাই ষষ্ঠী এর উদাহরণ।
পূণ্যিপুকুর ব্রত পালন করে গ্রামের কুমারী মেয়েরা। বাড়ির উঠানোর একটা জায়গায় ছোট একটা পুকুর তৈরি করে তাতে প্রতিদিন ভোর বেলায় জল ঢেলে, ফুল দিয়ে পুকুরের চারপাশে সাজিয়ে উপাসনা করেন তারা। চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু করে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে পালন করা হয় এই ব্রত। বিশ্বাস করা হয় এই ব্রত করলে কুমারী মেয়েরা তার মনের মতো বর পাবে।
এই ব্রতগুলো প্রান্তিক নারীদের জীবনে একটি আধ্যাত্মিক আশ্রয় হিসেবে কাজ করে। গ্রামের সীমিত সম্পদের মধ্যেও তারা এই আচারের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস ও শক্তি প্রকাশ করে।

ব্রতকথা: নারীর কণ্ঠস্বর
প্রতিটি ব্রতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি গল্প যাকে বলা হয় ব্রতকথা। এই কথাগুলো মুখে মুখে প্রচারিত হয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে যায়। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীতে বেহুলার অটল নিষ্ঠা, সাবিত্রী ব্রতের গল্পে সাবিত্রীর সাহস—এই গল্পগুলো নারীদের মধ্যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগায়। এই ব্রতকথাগুলো শুধু ধর্মীয় নয়, বরং নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অংশ। এগুলো প্রান্তিক নারীদের জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ, এবং স্বপ্নের প্রতিফলন।
উদাহরণস্বরূপ, সাবিত্রী ব্রতের কাহিনীতে সাবিত্রী তার স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য যমের সঙ্গে লড়াই করেন। এই গল্প প্রান্তিক নারীদের জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দেয়। ব্রতকথাগুলো নারীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ জাগায়, এবং তাদেরকে সমাজে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব বোঝায়।
ব্রত সামাজিক সংহতির মাধ্যম
গ্রামীণ সমাজে নারীরা প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদের জীবন ঘরের কাজ, সন্তান লালন-পালন, এবং পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ব্রত পালন তাদের একটি স্বাধীন স্থান দেয়। জামাই ষষ্ঠী, লক্ষ্মী পুজো, বা ইতু পুজোর মতো ব্রতগুলো নারীদের একত্র করে।
এই সময়ে তারা একে অপরের সঙ্গে গল্প করে, হাসি-ঠাট্টায় মেতে ওঠে, এবং তাদের দুঃখ-সুখ ভাগ করে নেয়। এই মেলামেশা তাদের মধ্যে একটি সংহতির বোধ তৈরি করে। এই সংহতি নারীদের জীবনে শক্তি যোগায়, তাদের একাকীত্ব দূর করে, এবং তাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়।
গ্রামীণ সমাজের যে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো সেখানে যেকোনো কিছুর জন্যই নারীদের স্বামীর থেকে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু এই একটা দিনেই তারা স্বামীর থেকে কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। একেবারে মেয়েলি ব্যাপার বলে কোনো স্বামীও এতে নাক গলানোর প্রয়োজন মনে করেন না। এতে করে নারীরা তাদের স্বকীয়তা একদিনের জন্য হলেও অনুভব করতে পারেন।
নারীর সৃজনশীলতার প্রকাশ
ব্রত পালনের মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে। লক্ষ্মী পুজোর সময় মাটির উপর ধান দিয়ে আঁকা আলপনা, সেজুতি ব্রতের সময় ফুল দিয়ে তৈরি নানা নকশা, বা ব্রতকথা গাওয়ার সময় তাদের কণ্ঠের মাধুর্য—এই সবই তাদের শৈল্পিক পরিচয়ের প্রতীক। আলপনা আঁকার সময় মনে হয় যেনো প্রতিটি নারী তার মনের আলপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে যাচ্ছে অনবরত। যেনো তৈরি করছে নিজের আলাদা একটা জগৎ।
হিন্দুবাড়িতে হয়তো দেখে থাকবেন পৌষ পার্বনের সময় আতপ চালের গুড়ো দিয়ে বাড়ির উঠান জুড়ে এক ধরনের আলপনা রয়েছে। এটা মূলত পৌষ পার্বনের সময় বাংলার নারীরা করে থাকে। এই শিল্পকর্মগুলো নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নত করে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ
ব্রত পালন নারীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই আচারগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য রক্ষা করে। উদাহরণস্বরূপ, পুণ্যিপুকুর ব্রতের সময় কুমারী মেয়েরা চার বছর ধরে নির্দিষ্ট আচার পালন করে, যা তাদের ভালো বিয়ের আশা জাগায়। এই ব্রতগুলো শুধু ধর্মীয় নয়, বরং নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে তুলে ধরে।
কথায় বলা হয় ‘হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বন’। মূলত এই তেরো পার্বনকে টিকিয়ে রাখে বাংলার প্রান্তিক নারীরা। তারা প্রতিমাসেই কোনো না কোনো ব্রত পালন করে থাকে।
ব্রতের শ্রেণিবিন্যাস
আবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: শাস্ত্রীয় ব্রত এবং অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রত।
শাস্ত্রীয় ব্রতগুলো ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে পালিত হয়, যেমন একাদশী বা শিবরাত্রি। অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলো লোকসংস্কৃতির অংশ, যা মূলত নারীরা পালন করে।
এগুলো আবার দুই ভাগে বিভক্ত: কুমারী ব্রত (৫-১০ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য) এবং নারী ব্রত (বিবাহিত নারীদের জন্য)।
উদাহরণস্বরূপ, পুণ্যিপুকুর ব্রত কুমারী মেয়েদের জন্য, যা তাদের ভালো বিয়ের আশা জাগায়, আর জামাই ষষ্ঠী বিবাহিত নারীদের জন্য, যা তাদের জামাইয়ের মঙ্গল কামনা করে।
স্বামী, সন্তান ও জামাইয়ের মঙ্গলকামনায় ব্রত
ষষ্ঠী ব্রত বাংলার অন্যতম পুরাতন এবং নারীকেন্দ্রিক ব্রতগুলোর একটি। তবে দেবী ষষ্ঠীর পূজো ঠিক কত প্রাচীন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, কারণ বেদ কিংবা প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। তবে পঞ্চম শতকের বায়ু পুরাণে ষষ্ঠী দেবীকে ৪৯ দেবদেবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অনেকে মনে করেন, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর মতোই ষষ্ঠী দেবীকেও লোকমনে প্রতিষ্ঠা দিতে পুরাণ রচয়িতারা তাঁর মাহাত্ম্য গড়ে তোলেন। ষোড়শ শতকে বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’-এও চৈতন্যের জন্মদিনে ষষ্ঠীর পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায়, এই পূজা বাংলায় আরও প্রাচীন।
ষষ্ঠী দেবী মূলত উর্বরতা, সন্তান-লাভ ও বংশ রক্ষার প্রতীক। বিশেষ করে সন্তান না হওয়া নারীর জীবনে মা ষষ্ঠী ছিলেন আশ্রয় ও আশ্বাসের প্রতীক। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে দেবীকে সন্তানহীনতার অভিশাপ মোচনের দেবী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
এই প্রেক্ষাপটেই উঠে আসে ‘জামাই ষষ্ঠী’র প্রথা। হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি ধারণা হল, মেয়ের বিয়ের পর যতক্ষণ না সে সন্তানসম্ভবা হয়, ততক্ষণ পিতামাতা তার বাড়িতে আহার করেন না। এর পেছনে রয়েছে ঋগ্বেদীয় ধ্যান—বিয়ের উদ্দেশ্য পুত্র সন্তান লাভ। ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী, পুত্রহীন স্বামীর স্বর্গপ্রাপ্তি দুর্লভ, এমনকি পূর্বপুরুষের পিণ্ডদানও পুত্র ব্যতীত অসম্ভব ধরা হয়। ফলে সন্তানহীনতা হয়ে ওঠে নারীর জীবনে এক ভয়াবহ সামাজিক চাপ।
এই চাপ প্রশমনের এক প্রতীকি রূপই হল মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ। শাশুড়িরা জামাইকে ডেকে ছয়টি ফল, পাখার হাওয়া এবং মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করেন এই বিশ্বাস থেকে যে, জামাইয়ের মাধ্যমে তাদের কন্যার মাতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। এটি শুধুমাত্র একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, বরং একটি সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, যা উর্বরতা, মাতৃত্ব এবং পারিবারিক উত্তরাধিকার রক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

ব্রত পালনের রীতি-নীতি: বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নারীর অংশগ্রহণ
ব্রতের শুরু হয় মানসিক প্রস্তুতি ও সংকল্প দিয়ে, যেখানে নির্দিষ্ট দেবতা ও নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে উপবাস, শুচিতা ও নিরামিষ আহারের আয়োজন থাকে।
ব্রত পালনের সময় ব্যবহার করা হয় নানা উপাচার—ধূপ, দীপ, ফুল, ফল, চাল, দুধ, পান-সুপারি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন। আলপনা আঁকা বা প্রতীক চিত্র আঁকার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় এক দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ। ব্রতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্রতকথা পাঠ ও গান, যা পৌরাণিক বা লোকাচারভিত্তিক কাহিনি থেকে উৎসারিত এবং যা নারীদের মধ্যে সামাজিক সংযোগও গড়ে তোলে।
এই আচার শুধু বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণ সংযম ও নিয়ন্ত্রণের অনুশীলনও বটে। উপবাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ব্রতের শেষে থাকে সমাপন পর্ব ও প্রসাদ বিতরণ, যা সামাজিক সংহতির প্রতীক। অনেক সময় দরিদ্র নারীদের দানও দেওয়া হয়, যা নারীর সহমর্মিতা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ।
সব মিলিয়ে, ব্রত নারীর আত্মপরিচয়ের সাংস্কৃতিক এক অঙ্গন, যা ধর্ম, সমাজ, সংস্কার এবং নারী-সম্প্রীতির এক অনন্য প্রতিফলন।
আধুনিক সময়ে ব্রতের প্রাসঙ্গিকতা
আধুনিক সময়ে শহুরে জীবনে ব্রত পালনের প্রচলন কিছুটা কমলেও, গ্রামীণ সমাজে এটি এখনও জনপ্রিয়। জয় মঙ্গলবার, জামাই ষষ্ঠী, বা লক্ষ্মী ব্রতের মতো আচারগুলো এখনও নারীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষিত ও স্বাধীন নারীরা এই ব্রতগুলোকে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন। তারা এটিকে ধর্মীয় আচারের চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পালন করেন। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও, ব্রত বাঙালী নারীদের পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
বাঙালী সমাজে ব্রত পালন প্রান্তিক নারীদের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ, এবং সামাজিক সংহতির প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ব্রতকথা, লোকাচার, এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে নারীরা তাদের শক্তি, সৃজনশীলতা, এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে। গ্রামের সেই কুয়াশা মাখা সকালে, যখন নারীরা একত্রিত হয়ে ব্রত পালন করে, তারা শুধু দেব-দেবীর পূজা করে না, তারা তাদের নিজেদের পরিচয়কে উদযাপন করে।
তথ্যসূত্র-
- https://www.ebanglalibrary.com/topics/3679/
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://othervoice.in/article/ov-7-4-24-6&ved=2ahUKEwiy5dXEvbeNAxWzR2wGHYcGDPwQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2E4SnqK61hKeQLAc7FfpEg
- https://www.boisoi.com/2020/10/blog-post_18.html
- https://www.prothomalo.com/onnoalo/books/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%9C%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0
- www.jagobangla.com
- www.banglapedia.org
- www.lokogandhar.com