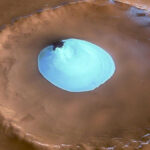বর্তমানে সাড়া জাগানো AI প্রযুক্তিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। প্রতারণামূলক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দিতে এবং অসঙ্গতিগুলোকে সনাক্ত করতে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে AI ব্যবহার করা যেতে পারে।
নির্বাচন এবং গণতন্ত্র বিষয় দুটিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, আসলে বিষয়টি মোটেও এমন নয় এবং কখনো ছিলও না। বরং, গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করার একটি রূপ হল নির্বাচন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে নির্বাচন ছিলো সীমাবদ্ধ, শ্রেণীভিত্তিক এবং ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি প্রক্রিয়া। প্রাচীন সময় থেকে আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভব পর্যন্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় এসেছে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন।
প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে। এর বিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে। নির্বাচন ব্যবস্থার শুরুর দিকে সব শ্রেণীর মানুষদের অধিকার ছিল না নির্বাচনের অংশ নেওয়ার। এ বিষয়ে সবার তেমন আগ্রহও ছিল না।
নির্বাচনের ইতিহাস
বিশ্বে নির্বাচনের ইতিহাস ও বিবর্তন একটি জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রাচীন নির্বাচনগুলো আধুনিক নির্বাচনের মতো ছিল না। মানব সভ্যতার শুরু থেকে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন ও ক্ষমতা বন্টনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এসেছে।
যেমন, প্রাচীন এথেন্সে লটারি ও সভার মাধ্যমে নির্বাচন, প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রে সেঞ্চুরিট অ্যাসেম্বলি (এখানে সেনাদের শ্রেণি অনুযায়ী ভোটগ্রহণ ও অভিজাত শ্রেণির ভোটের গুরুত্ব বেশি ছিলো), ক্রাইবাল অ্যাসেম্বলি (বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধিত্ব), ভারতের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, চীনে ম্যান্ডারিন পরীক্ষা যার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হতো, যারা জনশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো ।
প্রাচীন যুগ
প্রাচীন গ্রিস ও রোমে নির্বাচন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি হয়। সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত রোমান সম্রাট ও পোপের মত শাসক বাছাই করতেও নির্বাচন করা হতো। প্রাচীন ভারতেও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজারা রাজাদের বাছাই করতেন।
এথেন্সের নির্বাচন
এরপর গণতন্ত্রের সূচনা হতে দেখা যায় প্রাচীন এথেন্সে। প্রায় ৪০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সরকারের রূপ হিসাবে এখানে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের নাম ও ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল। প্রথমবারের মতো এথেন্সে সরাসরি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, যেখানে সাধারণ নাগরিকরা সরাসরি আইন প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তবে, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকরাই সরাসরি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতেন। এতে নারী, ক্রীতদাস এবং অভিবাসীরা অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

রোমের নির্বাচন
প্রাচীন রোমেও প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রে (৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২৭ খ্রিস্টাব্দ) নির্বাচনের মাধ্যমে সিনেট এবং অন্যান্য উচ্চ পদে কর্মকর্তা নির্বাচিত হতো, যদিও এখানে কেবল ধনী শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে নির্বাচন
মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় ভারতীয় উপমহাদেশে “জনপদ” নামে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল, যেখানে স্থানীয়ভাবে নির্বাচনের মতো কিছু ব্যবস্থা ছিল বলে মনে করা হয়। তবে এটি নির্দিষ্টভাবে নির্বাচন না হলেও জনসভার মাধ্যমে মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।
মধ্যযুগ
বাংলার মধ্যযুগের গোড়ার দিকে রশিদুন খিলাফৎ ও পাল রাজাদের মধ্যে গোপালকে বাছাই করতে নির্বাচন করা হতো। তবে, মধ্যযুগে নির্বাচনের ধারণাটা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। এই সময় সাধারণ জনগণের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণও সীমিত ছিল কেননা উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতা স্থানান্তরিত হতো। তখন শাসকগোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় এত বেশি পার্থক্য তৈরি হয়েছিল যে, সাধারণ জনগণের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে তেমন আগ্রহ ছিলো না ।
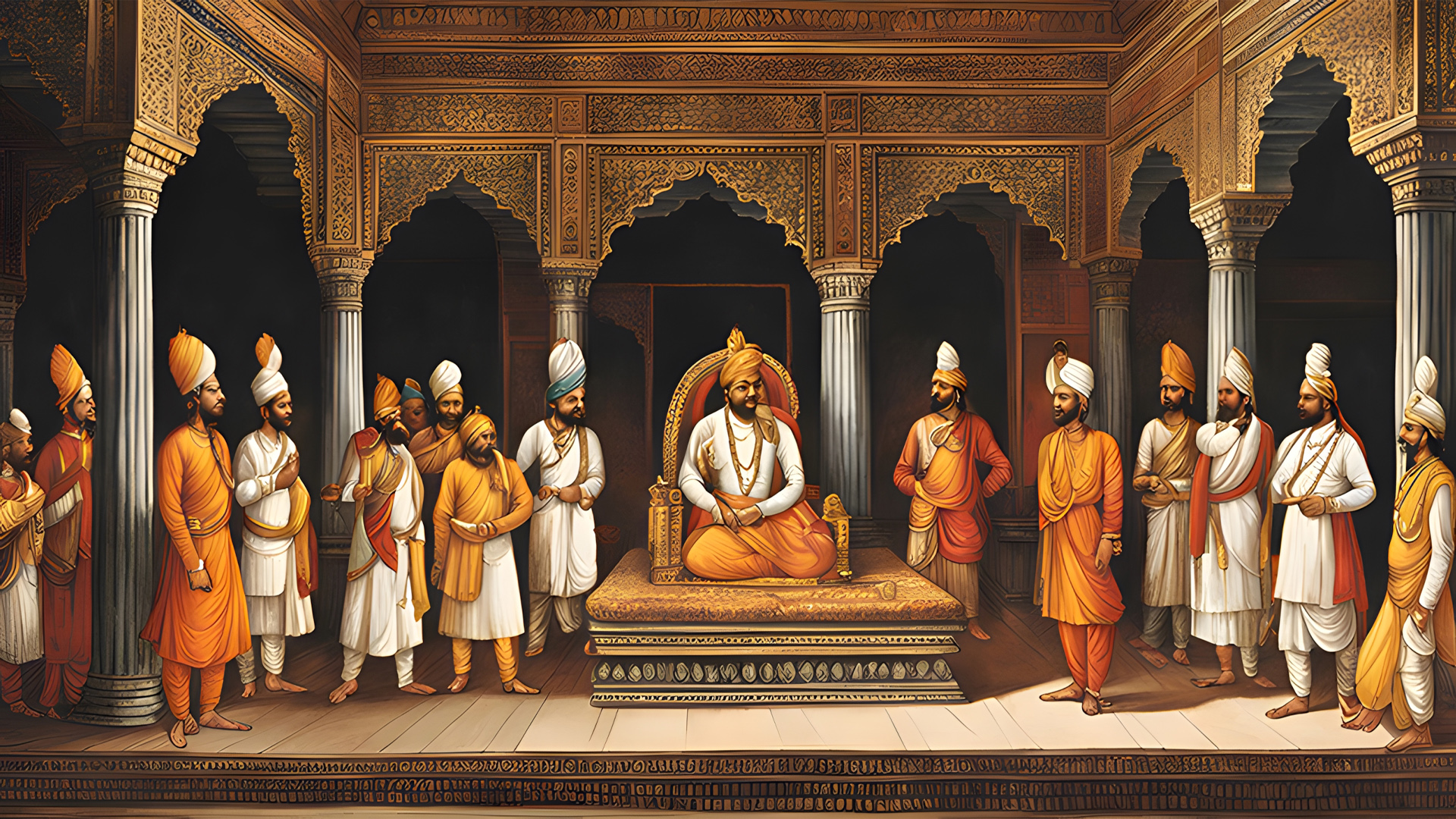
বর্তমানে বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
বর্তমানে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রধানত তিনটি জনপ্রিয় পদ্ধতির মধ্যে বিভক্ত:
- সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী (First-Past-The-Post),
- অনুপাতভিত্তিক পদ্ধতি (Proportional Representation), এবং
- মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Electoral Systems)।
এছাড়াও রয়েছে দুই-ধাপের নির্বাচন ব্যবস্থা (Two-Round System), পছন্দভিত্তিক ভোটিং (Preferential Voting)।
যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ব্যবস্থা
যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী (First-Past-The-Post) পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। সাধারণত কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও সিনেটর নির্বাচনে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। কিন্তু, তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় একটু ভিন্নভাবে। এখানে ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে ইলেক্টোরাল ভোট হয়ে থাকে।
যুক্তরাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থা
যুক্তরাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থাও First-Past-The-Post পদ্ধতি ভিত্তিক। হাউস অফ কমন্সের সদস্যরা নির্বাচিত হন একক আসনে একক ভোটের ভিত্তিতে, এবং যার ভোট বেশি, সেই জয়ী হয়। ফলে ছোট দলগুলোর জন্য সংসদে আসন পাওয়া কঠিন হয়। এই পদ্ধতিতে দুটি বড় দল কনজারভেটিভ এবং লেবার পার্টি বেশিরভাগ আসন দখল করে।
ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা
ভারতে সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। লোকসভা (সংসদের নিম্নকক্ষ) এবং বিধানসভা নির্বাচনেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি সংসদীয় আসনে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী জয়ী হন। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুপাতভিত্তিক পদ্ধতিতে (Proportional Representation) হয়, যেখানে ইলেকটোরাল ভোটের প্রাধান্য রয়েছে এবং সংসদ সদস্য ও বিধায়কদের মাধ্যমে ভোট হয়।
জার্মানির নির্বাচন ব্যবস্থা
জার্মানিতে মিশ্র নির্বাচন ব্যবস্থা (Mixed-Member Proportional Representation) ব্যবহৃত হয়। বুন্দেসটাগ (পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ) নির্বাচনে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এখানে ভোটাররা দুটি ভোট দেন। একটি তাদের একক আসনের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এবং অন্যটি তাদের প্রিয় রাজনৈতিক দলের জন্য। এতে দলীয় আসন সংখ্যার অনুপাত ধরে পরবর্তীতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়।
ফ্রান্সের নির্বাচন ব্যবস্থা
ফ্রান্সে দুই-ধাপের নির্বাচন ব্যবস্থা (Two-Round System) ব্যবহৃত হয়। প্রেসিডেন্ট এবং সংসদীয় নির্বাচনে প্রথম রাউন্ডে কোনো প্রার্থী যদি ৫০% বা তার বেশি ভোট পান, তিনি জয়ী হন। যদি না পান, তবে শীর্ষ দুই প্রার্থী দ্বিতীয় রাউন্ডে মুখোমুখি হন। এই পদ্ধতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বেড়ে যায় এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে জনগণের ভোটের মাধ্যমে একজন জয়ী হয় ।
জাপানের নির্বাচন ব্যবস্থা
জাপানের নির্বাচন পদ্ধতি হলো মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি, যা প্রধানত সংসদীয় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সংসদের নিম্নকক্ষে (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ) প্রথমভোট এবং অনুপাতভিত্তিক আসন বরাদ্দ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। এখানেও ভোটাররা দুইবার ভোট দেয়। একটি একক আসনের জন্য এবং অন্যটি দলভিত্তিক।
সুইজারল্যান্ডের নির্বাচন ব্যবস্থা
সুইজারল্যান্ডে অনুপাতভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা (Proportional Representation) অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির ফলে ছোট দলগুলোও পার্লামেন্টে আসন পেতে পারে। দেশটির গণতন্ত্র ব্যবস্থা অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক, যেখানে গণভোট বা “রেফারেন্ডাম” ব্যবহৃত হয়। ফলে, জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচন ব্যবস্থা
অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনে আদর্শ পছন্দভিত্তিক ভোটিং (Preferential Voting) ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ক্রমানুসারে তালিকা বা র্যাংকিং তৈরি করেন। যদি কোনো প্রার্থী প্রথম পছন্দে ৫০% বা তার বেশি ভোট না পান, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি পছন্দের ভোটগুলি গণনা করা হয়। এই পদ্ধতি ভোটারদের ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে।
নির্বাচন এবং প্রযুক্তি
গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথমে শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮-এর দশকে মৌখিক ভোটের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রথমদিকে আদালতে কণ্ঠে ভোট দেওয়া হতো। পরবর্তীতে, হাতে গণনা করা কাগজের ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা শুরু হয়, যা সেই সময়ে ভোট দেওয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল। প্রযুক্তির উন্নয়নে পরবর্তীতে নির্বাচনকে আরো সহজ করার চেষ্টা করা হয় ।

১৮৯০ এ যান্ত্রিক লিভার মেশিনের প্রবর্তনকে ভোটদানে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর পাঞ্চ কার্ড পদ্ধতি, সরাসরি-রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক (DRE) সিস্টেম এবং ব্যালট মার্কিং ডিভাইস (BMDs) ব্যবহার শুরু হয়। বিএমডিএস নির্বাচনের জন্য সর্বাধিক ব্যবহারকৃত একটি পদ্ধতি।
গণতন্ত্রে নতুনত্বঃ নির্বাচনে AI এর ব্যবহার
বর্তমানে সাড়া জাগানো AI প্রযুক্তি ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। প্রতারণামূলক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দিতে এবং অসঙ্গতিগুলোকে সনাক্ত করতে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করতে AI ব্যবহার করা যেতে পারে, যা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ভোটার জালিয়াতি বা যান্ত্রিক ব্যর্থতার মতো সম্ভাব্য সমস্যাগুলো আরও দ্রুত এবং কার্যকরভাবে তদন্ত করতে ভূমিকা পালন করবে।

শুধু ইতিবাচক দিকই নয়, এদিক থেকে বরং কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হতে হবে জনগণের। যেমন- সরকারি কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে, AI যে উৎসগুলো ব্যবহার করে ডাটা এনালাইসিস এর জন্য, তা ভরসাযোগ্য নাও হতে পারে। আবার ডিপফেক কনটেন্ট তৈরি করতেও AI ব্যবহৃত হচ্ছে যা সকলের সচেতনতার দাবিদার।
উপসংহার
নির্বাচন হোক প্রাচীন যুগে বা বর্তমান যুগে, এর গুরুত্ব জনপ্রশাসনে অদ্বিতীয়। তবে, এই নির্বাচন কি ধরনের হবে তা নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন বিতর্ক হয়েছে। এক পক্ষ নির্বাচনকে দেখে জনগণের মতামত প্রকাশের অধিকারের প্রতিফলন হিসেবে, আরেকপক্ষ দেখে অকার্যকর এবং ভন্ডামিপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে। তাদের মতে নির্বাচন প্রায়ই ক্ষমতাবান শ্রেণী বা দলগুলোর স্বার্থ রক্ষা করার হাতিয়ার। যেখানে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা গুরুত্বহীন। যুগে যুগে নির্বাচন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিবর্তনকে আরও জনকল্যাণমূলক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বস্তরে প্রচুর কাজ করা প্রয়োজন।
রেফারেন্স
গণতন্ত্রের ইতিহাস – উইকিপিডিয়া
Voting Technology: How New Tech is Being Used in the Election Process