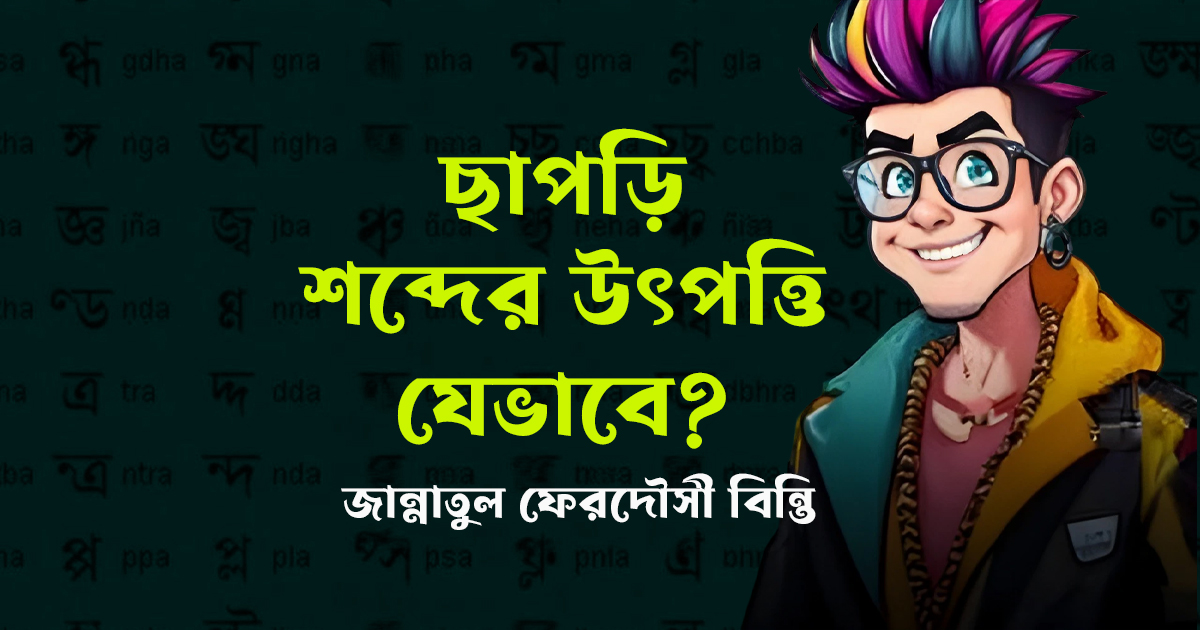“তুই ছাপড়ি, আমি ক্লাসি” এমনই ভাষা ব্যবহার করে ফ্যাশনের দুনিয়া এখন হয়ে উঠেছে নতুন এক রঙ্গমঞ্চ, যেখানে চলছে রুচি আর শ্রেণির দম্ভের লড়াই।
কয়েকদিন আগে হঠাৎ একটি শব্দ আমার চোখে পড়ল। শব্দটি হল ছাপড়ি । শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ অদ্ভুত লাগলেও, এর পেছনে রয়েছে গভীর ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও শ্রেণি-রাজনীতির ব্যাখ্যা।
মজার বিষয়, কিছুদিন আগেও এই “ছাপড়ি” শব্দটি অধিকাংশ মানুষের শব্দভাণ্ডারে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই এই শব্দটি তরুণ সমাজের মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করে। ঢাকার রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডায়, বিশেষ করে, সোশ্যাল মিডিয়ার মন্তব্যে যেন “ছাপড়ি” শব্দটি এক বিশেষ শ্রেণিকে নির্দেশ করে ব্যবহৃত হতে থাকে।
আজ আমরা এই ছাপড়ি শব্দের উৎপত্তি, জনপ্রিয়তা, সামাজিক প্রতিফলন এবং এর মধ্যে নিহিত রুচি ও ক্ষমতার রাজনীতি নিয়ে জানব।
ছাপড়ি শব্দের উৎস ও বিবর্তন
“ছাপড়ি” শব্দটি বাংলা ভাষার নিজস্ব কোনো শব্দ নয়। এটি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এক ধরণের আর্বান স্ল্যাং বা শহুরে অপভাষা। অনেকে আবার মনে করেন এটি হিন্দি, মারাঠি বা কন্নড় ভাষা থেকে এসেছে।
“ছাপড়ি” শব্দটির শিকড় মূলত “ছাপ্পাড়” শব্দে। মধ্যভারতের কিছু অঞ্চলে “ছাপ্পাড়” বলতে বোঝানো হয় কাঁচা ঘরের চালা বা ছাদ। বলা হয়, সেসময় ছাপ্পাড় নামক একটি জাতি বা পেশাজীবী গোষ্ঠী ছিল যাদের মূল কাজ ছিল মিস্ত্রির কাজ করা। বিশেষ করে ঘরের চালা ছাওয়া দেওয়া। তখন এই গোষ্ঠীকেই “ছাপড়ি” নামে ডাকা হতো। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে এই গোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যার কারনে তাদের সামাজিক অবস্থান আরও নিচে নেমে যায়।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির অর্থ ও প্রয়োগ বিবর্তিত হয়েছে। এখন এটি এমন এক ধরনের মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করতে ব্যবহৃত হয় যাদের চালচলন, পোশাক-আশাক বা জীবনধারা তথাকথিত মূলধারার সমাজের ‘রুচিশীলতা’র মানদণ্ডে পড়ে না। বিশেষ করে তরুণ সমাজে এই শব্দটি একটি সামাজিক গালি বা ঠাট্টার রূপে ব্যবহার হচ্ছে ।তাদের মতে ‘ছাপড়ি’ মানে হলো রুচিহীন, অশালীন ও অনুকরণপ্রবণ ফ্যাশনের প্রতিনিধি।
বাংলায় শব্দটির আগমন ও গ্রহণযোগ্যতা
বাংলা ভাষায় “ছাপড়ি” শব্দের ব্যবহারে শুরু কবে থেকে তা সুনির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও, ধারণা করা হয় যে, ২০২০ সালের দিকে ভারতীয় ইউটিউব ও টিকটক যুদ্ধের সময় এই শব্দটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।
মূলত সেই সময় ভারতের কিছু ইউটিউবার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী টিকটকারদের “ছাপড়ি” বলে গালি দিতে শুরু করে। আর তখন এই শব্দটি ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শহুরের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত জেন-জি, এই শব্দটিকে নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করণা।
শুধুই একটি শব্দ নাকি সমাজের একটি স্টেরিওটাইপ ধারনা!!
যেহেতু ছাপড়ি শব্দটি তরুণ সমাজের মধ্যে গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাই শব্দটিকে বেশ অপমানজনক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু শব্দটি শুধু একটি অপমানসূচক শব্দ নয়, বরং একটি গোটা স্টেরিওটাইপের প্রতিনিধিত্ব করে।
ছাপড়িদের কিছু বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ছাপড়িত্ব আছে বলে মনে করা হয়। মূলত ছাপড়িগণ তাদের ‘উদ্ভট’ ‘রুচি’র ফ্যাশনের জন্য ‘পরিচিত’। “ছাপড়ি” বলতে সাধারণত বোঝানো হয় এমন তরুণ তরুণীদের যারা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরে, খুব আটোসাটো বা ফিটিং হয় না এমন পোশাক পড়ে, চুলে রং করে, অস্বাভাবিকভাবে মোটরবাইকে স্টান্ট করে, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্তভাবে উপস্থিত থাকে। এদের বয়স সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আরও মনে করা হয় যে, তারা টিকটক ভিডিও বানায়ে থাকে। তাদের ফ্যাশন স্টাইল, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকি ভিডিও বানানোর ধরনকে ‘ক্রিঞ্জি’ বা হাস্যকর বলেই গণ্য করা হয়।

ট্যাকি, গাইয়া, ক্ষ্যাত: ছাপড়ির সমতুল শব্দগুলো
মজার বিষয় ছাপড়ি শব্দটি নতুন হলেও এর ধারণা বাংলা সংস্কৃতিতে একেবারে নতুন নয়। শুধু আগে ছাপড়ি শব্দের জায়গায় ব্যবহার হতো ‘বস্তি’, ‘ক্ষ্যাত’, ‘গাইয়া’, ‘গ্রামের চাচাতো ভাই’ ইত্যাদি শব্দগুলো। আবার আপনি যদি নিজেকে পশ হিসেবে দাবি করেন ,তাহলে হয়তো আপনি একই ধরনের ধারণা বোঝাতে ইংরেজিতে ব্যবহার করবেন ‘ট্যাকি’ বা ‘ক্রিঞ্জি’। এসব শব্দের মাধ্যমে সমাজে একটি শ্রেণিকে নিচু রুচির ও ‘নকলবাজ’ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়। কারন এই শব্দগুলোর মূল উদ্দেশ্যই থাকে সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে হাস্যকর ও অনুন্নত হিসেবে উপস্থাপন করা।
ছাপড়িত্ব: রুচির ব্যাখ্যা ও বিতর্ক
ছাপড়িত্ব নিয়ে প্রায়সময় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তার মূল কেন্দ্রে রয়েছে “রুচি” নামের একটি জটিল এবং নির্ধারণ করা কঠিন এমন ধারনা। জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার রুচিকে ব্যাখ্যা করেছেন “ব্যক্তিস্বভাব অনুযায়ী এক ধরনের প্রয়োজনবোধ” হিসেবে। অর্থাৎ কারও পছন্দ তার ব্যক্তিত্ব থেকে আসে, সেটি ভালো না মন্দ—তা নির্ধারণ করার একক মাপকাঠি নেই। তাহলে কোন ভিত্তিতে কাউকে বলা হয় “রুচিহীন”? কে ঠিক করে কোনটা উন্নত রুচি আর কোনটা ছাপড়িপনা?আদৌ কি এই বিতর্কের কোন ভিত্তি আছে?
রুচির শ্রেণি-রাজনীতি: পিয়েরে বোর্দিউ ব্যাখ্যা
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের তাকাতে হয় সমাজবিজ্ঞানী পিয়েরে বোর্দিউ তত্ত্বের দিকে। বোর্দিউ “রুচি”কে কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচি হিসেবে দেখেননি; বরং তিনি এটিকে দেখেছেন ক্ষমতার এক চর্চা হিসেবে। বোর্দিউ বলেন,
“সমাজে তিন ধরনের পুঁজি আছে: অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক। রুচি গড়ে ওঠে এই তিন পুঁজির সমন্বয়ে। অর্থাৎ কার কী পড়া উচিত, কী খাওয়া উচিত, কীভাবে কথা বলা উচিত এসব কিছু নির্ধারণ হয় কার পেছনে কী পরিমাণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি আছে তার ভিত্তিতে। “
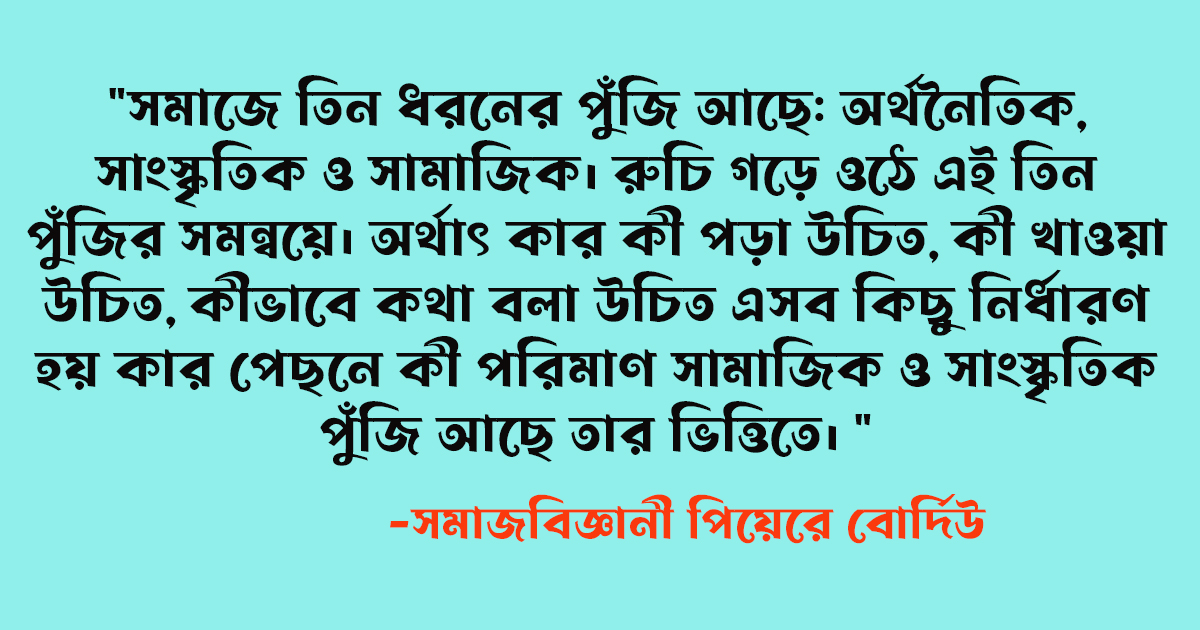
ছাপড়ি শব্দ ও শ্রেণিবিভাজনের প্রতিফলন
“ছাপড়ি” শব্দের ব্যবহার খেয়াল করলে দেখা যায়, এটি সাধারণত ব্যবহার করেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির তরুণরা। যারা নিজেদের ‘রুচিশীল’ বলে বিশ্বাস করে। আর যাদের উদ্দেশে শব্দটি ছোড়া হয়, তারা হয়তো আর্থিকভাবে নিম্নবিত্ত বা নতুন পয়সাওয়ালা। তারা মূলত চেষ্টা করে তথাকথিত “এলিট” স্টাইল অনুকরণ করতে কিন্তু পুরোপুরি রপ্ত করতে পারে না। ফলে তাদেরকে ‘wannabe’ অর্থাৎ অনুকরণকারী হিসেবে দেখা হয়। আর এই ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শ্রেণি-বিদ্বেষ ও ক্ষমতার সম্পর্ক।
রুচির লড়াই মানে নাকি স্ট্যাটাসের লড়াই
রুচি নিয়ে সমাজে বিবাদ নতুন কিছু নয়। কে কতটা উন্নত তা শুধু অর্থ দিয়ে নয়, রুচির মাধ্যমেও বিচার করা হয়। আসলে, আজকের সমাজে স্ট্যাটাস পেতে হলে কেবল টাকার জোরই যথেষ্ট নয়। সেই অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, কী ধরণের পোশাক পরা হচ্ছে, কীভাবে কথা বলা হচ্ছে, এমনকি কোথায় যাওয়া হচ্ছে এসব কিছুই গুরুত্ব পায়। ঠিক এখানেই এসে পড়ে ‘রুচি’র প্রশ্ন।
আর আশ্চর্যজনকভাবে এই রুচির লড়াই প্রায়শই এক ধরনের শ্রেণিচর্চায় রূপ নেয়। কিছু শব্দ এই লড়াইয়ে রীতিমতো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। “ছাপড়ি” ঠিক তেমন একটি শব্দ । এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় এমনভাবে, যেন কাউকে রুচিহীন, নিচু শ্রেণির বা ‘লোকাল’ বলে প্রমাণ করা যায়। এটি শুধু অপমানের নয়, বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে।এই শব্দের ব্যবহার সমাজের ভেতরকার শ্রেণি বৈষম্য, সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা এবং তথাকথিত “উচ্চ রুচির” মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্মোচন করে।
ভাষা কি ভাব প্রকাশ করে নাকি শ্রেণি নির্ধারণের হাতিয়ার?
ভাষাকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হলেও, বর্তমানে ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ।এটি সমাজে শ্রেণি বিভাজনের একটি শক্তিশালী অস্ত্র। প্রতিদিনের কথোপকথনের ভেতর দিয়েই ভাষা কখনো কখনো নিপীড়নের রূপ নেয়, হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক হিংস্রতার প্রকাশ।
“ছাপড়ি” শব্দটি তারই এক নগ্ন উদাহরণ। এই শব্দের মাধ্যমে সমাজের একটি শ্রেণি আরেক শ্রেণিকে হাস্যকর করে তোলে, অপমান করে, এবং সমাজে তার অবস্থানকে নিচু প্রমাণ করে। একইসঙ্গে, যারা এই শব্দ ব্যবহার করে তারা নিজেদের রুচিশীল, আধুনিক ও উচ্চতর শ্রেণিভুক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এটি নিছক অপমান নয় , বরং এটি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবির এক নিরব অথচ নির্মম ঘোষণা।
আর এই ধরণের ভাষাগত বিভাজন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামষ্টিক মনোভাবেও প্রভাব ফেলে। শব্দের ভেতর জমে ওঠে বৈষম্যের বিষ। আর সেই বিষই সমাজের ভেতরকার শ্রেণি-বিভক্তিকে আরও গভীর ও স্থায়ী করে তোলে।
ভাষার রূপান্তর ও হিন্দি-উর্দুর অনুপ্রবেশ: রুচির রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়
“ছাপড়ি” শব্দের বাংলা ভাষায় আগমন শুধু একটি শব্দগত পরিবর্তন নয় । শব্দটি একধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিফলনও ঘটিয়েছে। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সময়, সমাজ ও শ্রেণি চেতনার প্রতিচ্ছবি।
সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হলো,এক সময়ের প্রজন্ম যেখানে উর্দু ও হিন্দি ভাষার আগ্রাসন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।আজকের তরুণ প্রজন্ম সেই ভাষাগুলোর অসংখ্য শব্দ অনায়াসে গ্রহণ করছে। “হালদি নাইটি”, “সুকুন”, “বাবা কি পারি” এই ধরনের শব্দ এখন বাংলা কথ্য ভাষার অংশ হয়ে উঠেছে। মূলত সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব সিরিজ, বলিউড সংস্কৃতি এবং ইউটিউবের প্রভাবে এই অনুপ্রবেশ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।
এই ভাষার রূপান্তর নিছক শুধু শব্দের বিবর্তন নয়; এটি সাংস্কৃতিক দখলদারির একটি সূক্ষ্ম প্রকাশ। সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি এসব ভাষাকে গ্রহণ করে যেন একটি ‘আধুনিকতা’র প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে পারে। আবার, কেউ কেউ এই ভাষাকে রুচির অভাব হিসেবে দেখেন।
ফলে ভাষা হয়ে ওঠে শ্রেণিচিহ্নিত এক অন্তঃসত্তা । আর এর ফলেই এই একটি ছোট্ট শব্দ নির্ধারণ করে কে কতটা “আধুনিক”, কে কতটা “লোকাল”, কে কতটা “ছাপড়ি”। কি অদ্ভুত বিষয় তাই না?
ছাপড়ি হওয়া মানেই কি অপরাধ?
সবশেষে একটি অস্বস্তিকর, কিন্তু জরুরি প্রশ্ন তুলতে হয়, সেটি হলো “ছাপড়ি” হওয়া কি সত্যিই কোনো অপরাধ?
কারও পোশাক অন্যরকম হতে পারে, তার ফ্যাশন সেন্স প্রচলিত ‘ট্রেন্ড’-এর সঙ্গে না-ও মিলতে পারে, কিংবা তার কথা বলার ধরন, চলাফেরা, চুলের রঙ সবকিছুই আমাদের অনেকের চেয়ে আলাদা হতেই পারে। কিন্তু তাতে কি সে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়? সমাজে কি তার মূল্য কমে যায় ?
আর কাউকে শুধুমাত্র চেহারা, পোশাক বা উচ্চারণের ভিত্তিতে ‘রুচিহীন’ আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত? নাকি এটাই আমাদের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবোধ, সাংস্কৃতিক ঔদ্ধত্য এবং তথাকথিত আধুনিকতার মোড়কে লুকিয়ে থাকা বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ?
এই প্রশ্নগুলো আমাদের সামাজিক আচরণ, রুচি সংজ্ঞা ও ভাষাগত নিপীড়নের দিকে নতুন করে তাকাতে বাধ্য করে। আসলে ‘রুচি’ বলতে আমরা কী বুঝি, আর কেনইবা সেই বোঝার পেছনে এতো ক্ষমতার খেলা চলছে?
আমার নিজস্ব মতামত যার যেটা পছন্দ সে সেটা পড়তেই পারে আমি বা আপনি সেটা নিয়ে কথা বলার মত কেউ না। তাই সে স্বাভাবিক জামা পড়ুক আর আপনার চেয়ে অন্যরকম জামা পরুক আপনি সেটা নিয়ে কথা বলার কেউ না ।
“ছাপড়ি” শব্দটি কোনো সাধারণ স্ল্যাং নয়; এটি সমাজের শ্রেণি, রুচি ও ক্ষমতার ব্যবস্থার এক জটিল প্রতিফলন। এটি এক ধরণের সাংস্কৃতিক ছাঁকনি । যার মাধ্যমে কিছু মানুষকে নিচু, হাস্যকর ও ‘অযোগ্য’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গভীরে তাকালে দেখা যায়, যাদের ছাপড়ি বলা হয়, তারা হয়তো নিজস্বভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে চায়, হয়তো সমাজের স্টেরিওটাইপ ভেঙে কিছু আলাদা করে দেখাতে চায়। আর হয়তো সেই চেষ্টাকেই অনেকে রুচিহীন বলে থাকে।
আসলে, “রুচি” নামে যে জিনিসটিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার কোনও একক মানদণ্ড নেই। এটি সময়, শ্রেণি, শিক্ষা, পরিবেশ, অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ফলে কাউকে “রুচিশীল” বা “অরুচিশীল” বলার মধ্যেও থাকে এক ধরনের শ্রেণিবিদ্বেষ। “ছাপড়ি” শব্দের ব্যবহার সেই বিভেদকে আরও জোরালো করে তোলে।
সবশেষে আমাদের ভাবা উচিত আমরা আসলে কী প্রচার করছি? রুচির বিচার, না কি এক ধরনের শ্রেণি-নির্ধারিত সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা?
যাদের আমরা ‘ছাপড়ি’ বলে তাচ্ছিল্য করি, তারা হয়তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। শুধু ভিন্ন রুচির, ভিন্ন পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের। আজ যেটিকে আমরা নিচু স্তরের বলে মনে করি, একদিন হয়তো সেটিই হয়ে উঠবে সমাজের সময়ের মূলধারা।
রেফারেন্স:
- https://www.quora.com/What-is-the-meaning-of-Chhapri-How-are-people-defining-chhapri-nibba-or-nibbi
- https://www.earki.co/itsnotearki/article/9863/%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%8B
- https://en.wikipedia.org/wiki/Distinction_(sociology)